ভাষা আন্দোলন ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী
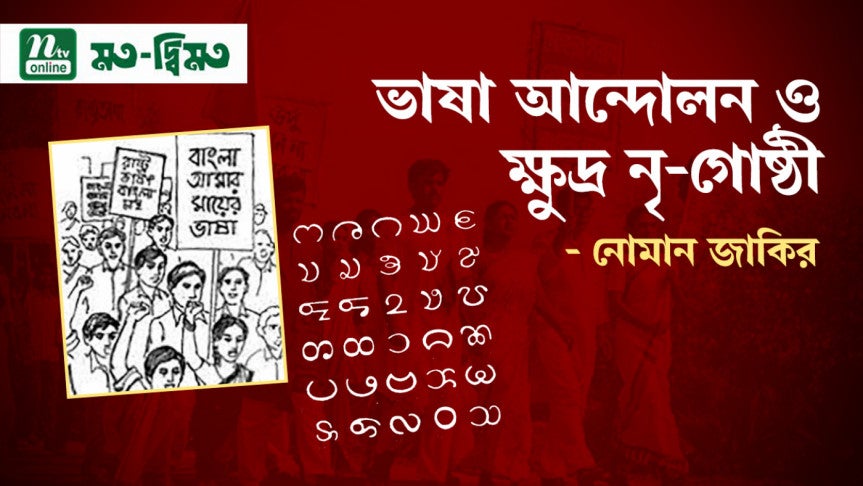
প্রস্তাবটি মূলত ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে উত্থাপন করা হয়। আর এতে ১৮৮টি দেশ সমর্থন জানালে বাংলাদেশে ’৫২ এর ভাষা আন্দোলনে শহীদদের শ্রদ্ধায় নিবেদিত একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। সেই থেকে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে ধারণ করে নিজ নিজ মাতৃভাষা লালনে সমগ্র বিশ্ব আজ ঐক্যবদ্ধ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মানব বিবর্তন বিভাগের শিক্ষক ও নৃবিজ্ঞানী রবার্ট ফোলি বলেন ‘জটিল যতো বিষয় আছে তার একটি এই ভাষা এবং এটিই আমাদের মানুষ বানিয়েছে’। মানুষের ভাব, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাসের বাহন হল তার মায়ের ভাষা। এ ভাষাতেই তার কথা বলা, স্বপ্ন দেখা, হাসি-কান্না, সুর ও সংগীত কিংবা বচন-নির্বচনীয় সব ধনের অনুভূতির বহি:প্রকাশ ঘটে। ভাষা হল সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম যা একটি জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনে এই অন্তর্নিহিত অনুধাবন প্রতিটি মানবসত্তার জন্য বিশেষভাবে জরুরি যা তাকে করবে প্রতিটি ভাষার প্রতি মননশীল ও শ্রদ্ধাশীল।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত গেজেট ২৩ মার্চ ২০১৯অনুযায়ী, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা মোট ৫০ টি। যার পরিক্রমায়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানবাধিকার রক্ষা সংস্থাগুলোর আপত্তি সত্ত্বেও (তাদের মতে নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা ৩০ লাখের মতো) হল ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৬ লাখ ৫০হাজার ১৫৯ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন (সূত্র: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, দ্য ডেইলি স্টার)। তবে, প্রতিবেদনে উল্লেখিত এই বিতর্কের সমাধান আজকের এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য নয়। এই প্রবন্ধ, ভাষা আন্দোলনের ফলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের জনক হিসেবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার প্রতি দায়বদ্ধতা ও তাঁদের ভাষা সুরক্ষার প্রতি ইংগিতপূর্ণ। ঐতিহাসিক ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ আন্দোলনে যে বাঙালী জাতি আজ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে , যে জাতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এর কর্ণধার হিসেবে সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত ,সে জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষাকে আমাদের মনশীলতা ও শ্রদ্ধাশীলতা দিয়ে সমমর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি কিনা, তা আমদেরই নির্ধারণ করতে হবে।
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার জন্য লড়াই
বিশ্বের দ্বিতীয় ভাষা শহীদের গল্প দিয়ে শুরু করছি। সুদেষ্ণা সিংহ(১৯৬৪- ১৬ মার্চ, ১৯৯৬) আদিবাসী ভাষাশহীদ এবং দ্বিতীয় ভাষা শহীদ। সুদেষ্ণা সিংহ ১৯৯৬ সনে ভারতের আসাম রাজ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা স্বীকৃতির আন্দোলনে শহীদ হন। আসামের বরাক উপত্যকায় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের দীর্ঘ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে১৬ই মার্চ একটি স্মরণীয় দিন।
১৯ অক্টোবর ২০২৩, দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে আমেরিকান ক্লাবে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর পণ্য নিয়ে মেলায় অংশপ্রহণকারীরা তাঁদের ভাষা, সুর ও লড়াইয়ের গল্প শুনিয়েছিলেন। বান্দরবানের বম জনগোষ্ঠীর উদ্দীপনামূলক গান, ম্রো সম্প্রদায়ের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর বাঁশির সুর, চাকমা, মারমা, ককবরোক, গোল্ডেন আওয়ার নামের একটি প্রকাশনা সংস্থার চাকমা, মারমা, ককবরোক, ম্রোসহবিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ঐতিহ্যবাহীবই, সুফল চাকমার আদং স্টলে বিভিন্ন ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কন দিয়ে বিভিন্নক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের নারীশক্তি ও ঐক্যের প্রতিচ্ছবি, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীরঅধিকারকর্মী এবং ‘গ্লোবাল অ্যান্টি-রেসিজম চ্যাম্পিয়নশিপ অ্যাওয়ার্ড২০২৩’ বিজয়ী রানি ইয়েন ইয়েন এর বক্তব্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাকে করেছে সকলের জন্য বোধগম্য ও অনুধাবনীয়।
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ
‘জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০’ আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষা শিক্ষার অধিকারের বিষয়টি প্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে । ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১০’ সকল আদিবাসী জাতির ভাষা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের কথা স্বীকার করেছে । উক্ত আইনের ৯নং অনুচ্ছেদে ‘সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত প্রত্যেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, কারুশিল্প, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করার’ কথা উল্লেখ রয়েছে।
এখন আমরা দেখবো, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তাদের বর্ণমালায় রচিত উল্লেখযোগ্য কিছু পাঠ্য-পুস্তক কংবা তাদের রচিত সাহিত্য নিয়ে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করবো।
- চাকমা
ঐতিহ্যবাহী চাকমা চিকিৎসাশাস্ত্র ‘চাকমা তালিক’ সম্পূর্ণই চাঙমা ভাষা ও বর্ণমালায় লিখিত । দেবপ্রিয় চাকমার ‘ফেবো’ নামে উপন্যাস চাঙমা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে ।
- মারমা (ম্রাইনমা)
বর্ণমালা শিক্ষার বই প্রকাশিত হয়েছে ।
- রাখাইন
রাখাইন ভাষার বর্ণমালার নাম রাখাইন এ্যাক্ষারা ।
- ত্রিপুরা
বর্ণমালা শিক্ষার বই প্রকাশিত হয়েছে ।
- মান্দি (গারো)
মান্দিদের আ.চিক ভাষার বর্ণমালা ‘আ.চিক থোক বিরিম’-এ এই পর্যন্ত মোট চারটি বর্ণমালা প্রস্তাবিত এবং প্রকাশিত হয়েছে ।
- মৈতৈ মণিপুরী
মৈতৈ মণিপুরীদের মৈতৈ লোন (মৈতৈ মণিপুরীদের ভাষা) এর বর্ণমালা মৈতৈ মেয়েক জনগোষ্ঠীর ভেতরে অল্প বিস্তর প্রচলিত ।
- লেঙাম
লেঙাম জাতির লেঙাম থপিরসইট নামে একটি বর্ণমালা প্রস্তাবিত হয়েছে এবং প্রকাশিত হয়েছে ।
- ম্রো
ক্রামা ধর্মের প্রবর্তক মেনলে ম্রো ‘ম্রোচেট’ নামের ম্রো ভাষার বর্ণমালা উদ্ভাবন করেছেন ।
- অলচিকি
১৯২৫ সনে পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু কর্তৃক উদ্ভাবিত সাঁওতালি ভাষার বর্ণমালা অলচিকি ভারতে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন পেলেও বাংলাদেশে এখনও প্রচলিত হয়নি অলচিকি । বাংলাদেশে রোমান, বাংলা নাকি অলচিকি হরফ ব্যবহার করা হবে এই নিয়ে এখনো বিতর্ক চলমান।
- মাহালী
২০০৬ সনে মাহালী ভাষার জন্য রোমান হরফের সমন্বয়ে পরিবর্তিত এক বর্ণমালা ‘মাহালে’ প্রকাশিত হয়েছে ।
- খাসি
রোমান হরফ নিজেদের মতো পরিবর্তন করে ‘আ-বি-কে’ নামের বর্ণমালাটি নিজেদের ভেতর ব্যবহার করতে দেখা যায় ।
- কোচ
বাংলা হরফ ব্যবহার করে মাতৃভাষা শিক্ষার বই প্রকাশিত হয়েছে ।
- হাজং
আসাম ও বাংলাদেশ উভয় প্রান্তে বাংলা হরফকে ব্যবহার করেই বেশ কিছু হাজং প্রকাশনা রয়েছে ।
- বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী
ভারতের আসাম রাজ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির জন্য শহীদ হয়েছেন সুদেষ্ণা সিংহ ।
- কোল
বাংলা হরফ ব্যবহার করে রাজশাহী অঞ্চলে ছোট পরিসরে কোলদের ভেতর প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে কোল ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম বেসরকারি উদ্যোগে কিছুটা চলছে।
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অর্জন
চাকমা কবি ও লেখক মৃত্তিকা চাকমা ‘বাংলা একাডেমি পুরস্কার’ অর্জন করেছেন ।
মান্দি সমাজের শেরানজিংপালা, রেরে, আজিয়া, চাকমাদেররাধামন-ধনপুদি বা মৈতৈ ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের রাসপালা, ম্রোরূপকথা, ওঁরাও ও সাঁওতালি কাহিনী পালা আখ্যান, হাজংদেরদেবী দূর্গাপালার মতো আদিবাসী জনগণের রয়েছে অবিস্মরণীয় সব মৌখিক আখ্যান ।
‘গ্লোবাল অ্যান্টি-রেসিজম চ্যাম্পিয়নশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০২৩’ বিজয়ী হয়েছিলেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার কর্মী রানি ইয়েন ইয়েন।
চেতনাবোধ ও সংকল্প
ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে; কিন্তু বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় বেঁচে থাকা অন্য ভাষাগুলোর কথাও আমাদের ভাবতে হবে। বহু সংস্কৃতির এই বিশ্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী ভাষার অস্তিত্বই কেবল স্বীকার করব, তা হতে পারে না। আমাদের বাংলাদেশেই আছে অনেকগুলো ভাষা; এই ভাষিক বাস্তবতাকে স্বীকার করতে হবে।বাঙালিকে জানতে হবে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, হাজং ও সাঁওতালরা কী লিখছে। কেননা, বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রসীমার ভেতরে ভাষাগুলো সচলভাবে টিকে আছে। খুব আশান্বিত হই, যখন একজন চাকমাভাষী কবি ও নাট্যকার বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন।কিংবা বৈশ্বিক কোনো খেতাবে আমাদের করেন গৌরবান্বিত। একুশের চেতনা এই স্বীকৃতির কথা বলে; অঞ্চল, দেশ ও রাষ্ট্রের সবাইকে করতে চায় অংশীজন।
একুশ আমাদের যে চেতনা ও মূল্যবোধ উপহার দিয়েছিল—তা ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, স্বৈরাচারের পতনকার্যে একতাবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করতে, নিপীড়িত জনগণের পাশে এসে দাঁড়াতে ও সর্বোপরি মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে। একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে আমরা এক অকৃত্রিম আবেগের সৌধ নির্মাণ করেছি। যার সাথে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও জাতি চেতনামূলক আন্দোলনের চালিকা কেন্দ্র হয়ে আছে সর্বত্র। প্রতিটি গণ-আন্দোলনের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে ভাষা আন্দোলন।
একুশের তাৎপর্যকে ধারণ করতে হলে ভাষা আন্দোলনের মূল চেতনা আধিপত্যবাদ বিরোধী চেতনা ও শক্তির দিকে আমাদের ফিরে তাকাতেই হবে। সেখানেই আমাদের মুক্তি নিহিত।
আর সুখী-সমৃদ্ধ-উন্নত আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে এ মুহূর্তে জাতির সব ভেদাভেদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হিংসা-হানাহানি ভুলে এক অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্পপন্থা আছে বলে আমাদের জানা নেই। একুশের চেতনা হলো ভাষার অধিকার, কথা বলার অধিকার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার। এসবের উপস্থিতির অর্থ হলো, একুশের চেতনা সক্রিয়; আর অনুপস্থিতির মানে হলো, একুশের চেতনা অস্তিত্বহীন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হল আমাদের সেই চেতনার আয়না।
লেখক : উপ-পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রাজশাহী।























 নোমান জাকির
নোমান জাকির
















