শান্তনু কায়সার : বিপরীত স্রোতের লেখক
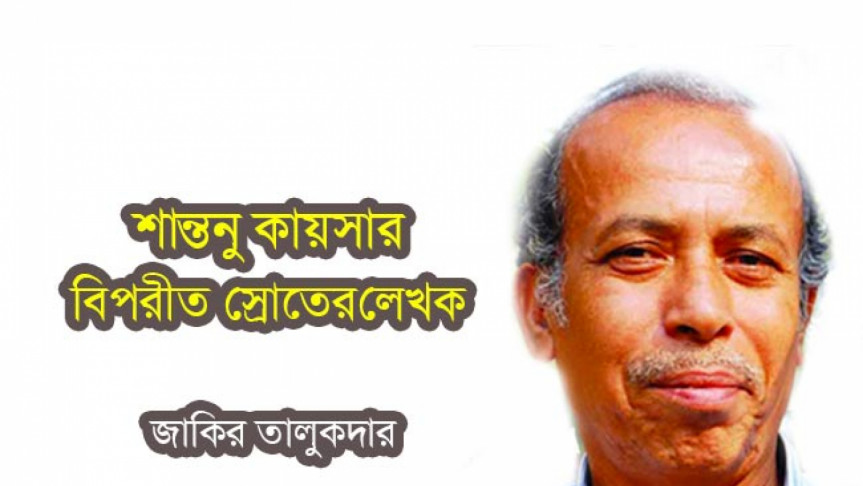
সাহিত্য তাঁর কাছে ছিল সাধারণ মানুষের মুক্তির সংগ্রামের সহযোদ্ধা।
এই বাক্যে একটি ভুল বোঝার অবকাশ রয়ে যায়। কেননা, জনগণের সাহিত্যের নামে এত বেশি স্লোগানসর্বস্ব লেখালেখি হয়েছে আমাদের ভাষাতে, যে কেউ জন ও জীবনমুখী সাহিত্যকর্মী হিসেবে পরিচিত হলেই তার গায়ে সেই স্থূল ও যান্ত্রিক লেখকের তকমা লেগে যায়। এটি আমাদের দেশের কলাকৈবল্যবাদীদের প্রবণতা। প্রথম দল দাবি করে—সাহিত্য হচ্ছে জীবনের জন্য। দ্বিতীয় দল দাবি করে—সাহিত্য হচ্ছে শিল্পের জন্য। শান্তনু কায়সার সেই বিরল লেখকদের মধ্যে একজন যিনি বলতে পেরেছিলেন এবং রচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন যে ‘সাহিত্য একই সঙ্গে জীবনের জন্য এবং শিল্পের জন্য’।
কাজটি সহজ নয়। সহজ নয় বলেই শান্তনু কায়সার খুবই সংখ্যালঘু একটি সাহিত্যিক-প্রবণতার উত্তরসূরি। সোমেন চন্দ, রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, সরদার ফজলুল করিম, আবু জাফর শামসুদ্দীন, শওকত আলী, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। আর বেশি নাম খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। আমাদের দেশের যে ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল সাহিত্যধারাটি মূলধারা হিসেবে পরিগণিত, শান্তনু কায়সার সেই মূলধারার অংশ হয়েও কিছুটা দূরবর্তী ছিলেন চিন্তার দিক থেকে। চিন্তার এই পার্থক্যটি সৃষ্টি হয়েছে কিছু মৌলিক চিন্তা এবং বিতর্ককে কেন্দ্র করে। মূলধারার লেখক-কবিরা একসঙ্গে সদর্থক অর্থেই বলে থাকেন যে বাংলাদেশ একটি একক জাতি-রাষ্ট্র। বাঙালির জাতি-রাষ্ট্র। কিন্তু শান্তনু কায়সার বলতেন আমরা একক জাতি-রাষ্ট্র নই। এই দেশে বাঙালি ছাড়াও অনেকগুলি ভিন্ন নৃতত্ত্ব এবং ভাষার মানুষ রয়েছেন। তারা জাতি হিসেবে আলাদা, কিন্তু এই বাংলাদেশের অখণ্ড অংশ। তাই তাদের ওপর বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দিতে গেলে তা হবে একটি নতুন ধরনের আধিপত্য। যে বাঙালি শত শত বছর ধরে নিজের ভাষা এবং জাতিসত্তা রক্ষার জন্য লড়াই করে এসেছে, সেই বাঙালি অন্য জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা ও জাতিসত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে, এটি মেনে নিতে নৈতিকভাবে রাজি ছিলেন না শান্তনু কায়সার।
হাজার বছরের অত্যাচারিত-নিপীড়িত বাঙালি অন্য ক্ষুদ্র আদিবাসীদের ওপর নিপীড়নকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে তা বাঙালি জাতির জন্য অপমানজনক বলে মনে করতেন শান্তনু কায়সার। তাই তাঁর কলম বছরের পর বছর সোচ্চার থেকেছে আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকারের পক্ষে। লেখককে এই রকম অবস্থান কখনো কখনো নিতে হয় ভুল গণপ্রবণতার বাইরে বিপরীতে। আলজিরিয়া ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশ। আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজের দেশ ফ্রান্সের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন দুই মহান লেখক জাঁ পল সার্ত্রে এবং আলবয়োর কামু। তাঁরা লিখেছেন আলজেরিয়ার ন্যায্য স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে, চেষ্টা করেছেন জনমত গঠন করতে, এমনকি বিপ্লবীদের অস্ত্র সংগ্রহের জন্য টাকাও পাঠিয়েছিলেন। দেশের মানুষের চোখে দেশদ্রোহী হবার আশংকা নিয়েও তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন সর্বমানবিক ন্যায়ের পক্ষে। আমাদের অতটা করতে হয় না। কিন্তু যা করা হয়, সেটিকেও হুমকি বলেই মনে করে শাসকগোষ্ঠী। তাই শান্তনু কায়সারের মতো লেখকরা আরো কোণঠাসা, আরো সংখ্যালঘু হয়ে পড়েন।
দ্বিতীয় চিন্তাপার্থক্য ভারতকে নিয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত রাষ্ট্র এবং ভারতীয় জনগণের সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশের অন্য সব মানুষের মতো তিনিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ছিলেন অকুণ্ঠ। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের আধিপত্যবাদী ভূমিকার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সচেতন। অন্ধ ভারতপ্রেম নয়, অন্ধ ভারতবিদ্বেষ নয়— ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের ব্যাপারটিকে তিনি দেখতে চাইতেন দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিতে। বড় পুঁজি ছোট পুঁজিকে শোষণ করবে— এটা স্বাভাবিক কথা। তাই ছোট পুঁজির দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিভিন্ন খাতকে নানা ধরনের প্রোটেকশন দিতে হবে। কিন্তু সরকারগুলোর মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে আমাদের দেশকে ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত করার নির্বোধিতাকে সমালোচনা করতেন তিনি। ভারতকে ট্রানজিট দেবার নাম করে তিতাস নদীকে ভরাট করে সড়ক তৈরিতে ব্যথাহত ছিলেন। ব্যথিত ছিলেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ‘সীমান্ত হত্যা’র বিষয়ে। পানিবণ্টন চুক্তিকে বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রাখছে ভারত। আমাদের সরকার এবং মিডিয়া একতরফাভাবে বছরের পর বছর প্রচারণা চালিয়ে মানুষের মনে এই চিন্তাটা ঢুকিয়ে দিতে চায় যে, ভারতের করুণা ছাড়া আমাদের ন্যায্য পাওনা পাওয়া যাবে না। রাষ্ট্রচালকদের এই নতজানু ভূমিকার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তিনি। তবে দুই দেশের শোষিত এবং বঞ্চিত মানুষের মধ্যে মৈত্রী এবং সহযোগিতার ব্যাপারে জোর দিতেন শান্তনু কায়সার। তার বিশ্বাস ছিল, দুই দেশের মেহনতি সাধারণ মানুষ একত্রিত হলে নিজ নিজ দেশের সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে দুই দেশের মধ্যে একটি সম্মানজনক এবং সুষম সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে।
মজার ব্যাপার এই যে প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়েও তার ভিন্নমত ছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে তিনি যেকোনো ধরনের মধ্যবর্তিতার বিপক্ষে ছিলেন। রাষ্ট্রকে হতে হবে সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্ম ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিষয়। রাষ্ট্র কোনো ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না, আবার কোনো ধর্মের বিরুদ্ধাচরণও করবে না। বাস্তবতার নামে বঙ্গবন্ধু থেকে শুরু করে আমাদের দেশের সকল রাষ্ট্রনায়কই এ ক্ষেত্রে আপস করেছেন। তারা সকল ধর্মকেই রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার আওতায় এনেছেন। বামদলগুলোর বাইরে একমাত্র আওয়ামী লীগই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে। কিন্তু আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা না করে বরং পৃষ্ঠপোষকতার নামে রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছে। তাই আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে শান্তনু কায়সার বলতেন যে, তারা আসলে ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা পরিবর্তন করে দিয়ে প্রকারান্তরে পরোক্ষভাবে ধর্ম নিয়ে রাজনীতিই করে যাচ্ছেন।
এই ধরনের বেশকিছু মানসিক এবং তাত্ত্বিক পার্থক্য সত্ত্বেও তিনি দেশের সকল প্রগতিশীল চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে এসেছেন সবসময়। মতের অমিল থাকলেই অন্যদের কাজকে গুরুত্বহীন বলে প্রচার করার প্রবণতা রয়েছে আমাদের মধ্যে। শান্তনু কায়সার এই যান্ত্রিক বিরোধিতার বাইরে থাকতে চেষ্টা করতেন। অন্য যারাই কোনো প্রগতিশীল আন্দোলন বা সংগঠন করেছেন, তাদের কাজের গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি। এই কথার প্রমাণ রেখেছেন নিজের কর্মের মধ্য দিয়েই। একদিকে যেমন ছিলেন বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের সক্রিয় কর্মী ও সংগঠক, আবার একই সঙ্গে কাজ করেছেন রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলন পরিষদের একজন হয়ে।
০২.
‘শ্রীনাথ পণ্ডিতের প্রাণপাখি’ নামের মৌলিক গল্পগ্রন্থ রয়েছে শান্তনু কায়সারের। এর বাইরেও রয়েছে বেশকিছু সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম। কিন্তু তিনি মূলত পরিচিত ছিলেন প্রাবন্ধিক, চিন্তাবিদ, গবেষক, এবং সাহিত্য-বিশ্লেষক হিসেবে। অন্যেরা তাকে চিহ্নিত করেছিলেন বামপন্থি লেখক বলে। নিজেও কখনো অস্বীকার করেননি বামপন্থার প্রতি তার আস্থার কথা। আবার যান্ত্রিক বামচিন্তা যে প্রকারান্তরে একজন সৃষ্টিশীল মানুষকে বন্ধ্যা বানিয়ে ছাড়ে, সে বিষয়েও ছিলেন সজাগ। অন্তত নিজে সেই চোরাফাঁদে আটকা পড়েননি কখনো। গণমানুষের সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু তার জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া সাহিত্য-সম্পাদকগুলিকে সামন্তবাদী বা পুঁজিবাদী সাহিত্যের তকমা লাগিয়ে ছুড়ে ফেলতে হবে, এমন মূঢ়তা কখনো প্রশ্রয় পায়নি তার কাছে। এ ক্ষেত্রে মাও সে তুং-এর সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে সাযুজ্য লক্ষণীয়—‘অতীতের শিল্পসাহিত্যের ভালো ও সুন্দর জিনিসগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। সেসবের মধ্যে যা কিছু কল্যাণকর সবই বিচার বিবেচনার মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করতে হবে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অতীতের সম্পদ ও বিদেশীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে বর্জন করা কিংবা সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা কোনোক্রমেই আমাদের উচিত হবে না।’ এই চিন্তার সঙ্গে যোগ করতে হবে ক্লাসিকত্ব পেয়ে যাওয়া রচনা এবং লেখকদের কথা। সেই বিবেচনাতেই শান্তনু কায়সার নিমগ্ন হন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা মীর মশারফ হোসেনের রচনা এবং কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণে। রচিত হয় ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ এবং ‘তৃতীয় মীর’। এই গ্রন্থ দুটি একাডেমিশিয়ানদের গবেষণাগ্রন্থগুলোর মতো ‘বই থেকে লেখা বই’ নয়। শান্তনু কায়সারের মৌলিক চিন্তা এবং পর্যালোচনার চিহ্ন বহন করছে ভেতরে ও বাহিরে।
রবীন্দ্রউত্তর সময়কালে এই উপমহাদেশে বামপন্থার পশ্চাৎপদতা এগুতে দেয়নি রেনেসাঁকে। বামপন্থিদের এই ব্যর্থতার পোস্টমর্টেম করতে চাইতেন শান্তনু কায়সার। খুঁজে পেয়েছিলেন সাম্প্রদায়িকতার প্রাদুর্ভাবকে। শ্রেণিদ্বন্দ্বকে সামনে আনতে পারেনি বামপন্থিরা। এখনো প্রগতি বারবার প্রতিহত হয় সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা। সেই কারণে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সম্পন্ন করতে পারেননি কাজটি। বিভিন্ন সময়ে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। আলোচনা হয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কখনো দিনের পর দিন। সেইসব আলাপের সারবস্তু যতটুকু মনে আছে, তা গুছিয়ে লিখলে এই রকম দাঁড়াবে—
সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে যেসব পাঠের সঙ্গে আমরা পরিচিত, আজ এই একবিংশ শতকে এসে দেখা যাচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত অবস্থা তার চাইতে অনেক বেশি ভয়াবহ। এখন জানা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার উৎস আমাদের চিন্তার চাইতে অনেক বেশি দূরবর্তী, ভিত্তি অনেক বেশি দৃঢ়, ইতিহাস অনেক বেশি প্রাচীন, ব্যাপ্তি আমাদের কল্পনার চাইতেও বেশি। অবস্থা যখন এতটাই ভয়াবহ, তখন তার অনুপুঙ্খ পাঠ না থাকলে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী কর্মপন্থা নির্ধারণ অপ্রতুল এবং কখনো কখনো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।
আমরা ভাবতে পছন্দ করি যে এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস খুব বেশি পুরনো নয়, ইংরেজ আমলেই তার আমদানী। আমরা এই ভেবেও নিজেদের প্রবোধ দিয়ে থাকি যে সাম্প্রদায়িকতা নিতান্তই সমাজের ওপরের বা রাষ্ট্রীয় স্তরের ব্যাপার, এবং আমাদের দেশের বা পার্শ্ববর্তী দেশের মাধারণ মানুষ, যাদের আমরা জনগণ বলে থাকি, তারা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে মুক্ত। কিন্তু এখনকার বাস্তবতা জানাচ্ছে যে সাধারণ মানুষ, সমাজের সবচাইতে নিম্নস্তরের মানুষও বিভিন্ন মাত্রার সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন। আর ইতিহাসপাঠ জানাচ্ছে যে ইংরেজ আগমনের অনেক আগে থেকেই সাম্প্রদায়িকতা এই উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, তার শিকড় ইতিহাসের অনেক গভীরে প্রোথিত। ইতিহাস অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যা হওয়ার কথা ছিল শ্রেনীদ্বন্দ্বের ইতিহাস, তা এই উপমহাদেশে পরিণত হয়েছে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাসে।
এই উপমহাদেশে বস্তুত সাম্প্রদায়িকতার শুরু সেই আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বের সময় থেকেই। বহিরাগত, আগ্রাসী, এবং বিজয়ী আর্যরা প্রথমেই আর্যাবর্তকে বেঁধে ফেলেছিল বর্ণাশ্রম নামের সাম্প্রদায়িকতায়। এই মাটির সর্বপ্রাণবাদী ধর্মসমূহ আর্যদের বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তুলনায় অনুন্নত বলে ঘোষিত হলো। বিজয়ী আর্যদের কাছে এই মাটির সন্তানরা ছিল দাস এবং দস্যু। আর্যদের আগমনের পূর্বে এই উপমহাদেশে ‘দাস’ শব্দটি ছিল অচেনা। ঋগবেদে এসে দেখা যাচ্ছে রাজা ‘গরু ঘোড়া ও দাস বিতরণ করছেন’। এমনকি ঋগবেদে পশু শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে, যেখানে দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা হচ্ছে। আর একবার দাস তো চিরকালীন দাস। ব্রাহ্মণ ঘোষণা দিচ্ছেন—‘স্বীয় প্রভু যদি শূদ্রকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দেন তাহা হইলেও শূদ্র দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় না; কারণ দাসত্ব তাহার স্বভাবজাত, কে তাহা লঙ্ঘন করিতে পারে?’
বর্ণাশ্রমকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া সম্ভববই নয়, কারণ বর্ণাশ্রমের বিধানসমূহ আসছে ধর্মগ্রন্থ থেকে। চতুর্বর্ণেরও বাইরে যে চণ্ডাল, তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে—‘কোনো চণ্ডালকে স্পর্শ করা, তার সঙ্গে কথা বলা বা তার দিকে তাকানোও পাপ। তাকে স্পর্শ করলে শুদ্ধ হবার জন্য সারা শরীর ডুবিয়ে স্নান করতে হবে। তার সঙ্গে কথা বললে (পবিত্র) ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা বলতে হবে; আর তার দিকে তাকালে সূর্যরশ্মির দিকে তাকিয়ে থেকে চোখের পাপ স্খালন করতে হবে।’ এমনকি ‘কোনো শ্রাদ্ধের উৎসর্গীকৃত সামগ্রী যদি চণ্ডাল ও অন্য অন্ত্যজরা দেখে ফেলে তাহলে তা অপবিত্র হবে।’
ব্রাহ্মণ্যবাদ ‘আর্য’ শব্দের অর্থ নির্ধারণ করেছিল—সুন্দর, সভ্য, কৃষ্টিবান। অন্যদিকে ভূমিপুত্র অনার্য মানেই—দাস এবং দস্যু। অধ্যাপক কোশাম্বি যাদের বলেছেন উদ্বৃত্ত বা সারপ্লাস সৃষ্টিকারী শ্রেণী। তাদের শ্রম নিয়োজিত হচ্ছিল জমিতে, কিন্তু ফসল ভোগের অধিকার ছিল কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের।
এই আর্য সাম্প্রদায়িকতার পাল্টা প্রতিবাদ হিসেবে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল লোকায়ত দর্শন। লোকেষু আয়তোঃ—জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই এই দর্শনের নাম লোকায়ত। এই লোকায়ত বিপ্লবীরা প্রচার করলেন—‘অজ্ঞ পৌরুষহীন অকর্মণ্য পুরোহিত সম্প্রদায়ের জীবিকার উপায় করে দেবার জন্যই তৈরি হয়েছে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের মন্ত্র, তিন তিনটি বেদ’। তারা আরো বলতে শুরু করলেন যে—‘আসলে স্বর্গ পারলৌকিক আত্মা বলে কিছু নেই’।
স্বভাবতই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় অক্ষশক্তি এদের দমন করেছিল নির্মমভাবে।
পরবর্তী বিদ্রোহ এসেছিল অনেক শত বৎসরের পরে বৌদ্ধধর্মের হাত ধরে। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়—‘প্রাচীন আর্য সমাজে ব্রাহ্মণদিগের প্রবল প্রতাপে হীন জাতি সকল যখন কাঁপিতে লাগিল, রাজাদের শক্তি পর্যন্ত যখন নামেমাত্র পরিণত হইল, আধ্যাত্মিক দাসত্বে প্রজাকুলের মনুষ্যত্ব যখন বিলীন হইল, মানব যখন পশুপ্রায় হইয়া পড়িল..’ সেই সময় বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব।
আদি বৌদ্ধধর্ম ক্ষত্রিয়দের দ্বারা প্রবর্তিত হলেও তার প্রধান ঝোঁক ছিল জনসাধারণের দিকেই। বস্তুবাদ এবং সাম্যের প্রবণতা ছিল অনেকখানিই। ব্রাহ্মণ্যবাদের অনেক মনগড়া তত্ত্বের সরাসরি বিরোধিতা করেছিল বৌদ্ধধর্ম। প্রাণীহত্যার বিরোধিতা করা ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রধান স্তম্ভ। ‘তাহারা বলে ছাগল আদি পশুকে মন্ত্র দ্বারা পবিত্র করিয়া যজ্ঞে বধ করিলে তাহারা স্বর্গে যায়। যদি স্বর্গে যাইবার পথ ইহাই হয়, তবে তাহারা তাহাদের বাপ-মা-ভগিনীদের সেই উত্তম পথে স্বর্গে পাঠাইয়া দেয় না কেন?’
প্রথম পর্বের নির্ভেজাল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে ব্রাহ্মণ্য পূজা-অর্চনা সম্পূর্ণই বর্জিত হয়েছিল। ব্যাপক জনতার প্রিয় উৎসবগুলিই স্বীকৃতি পেয়েছিল গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মে। এই দুই ধর্মকে দুটি শ্রেণীর মানুষ বরণ করেছিল সাগ্রহে। শূদ্র তো বটেই, তাদের সঙ্গে বৈশ্যরাও।
হিন্দু ধর্মের তাত্ত্বিকরা বলে থাকেন যে বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস করে নিয়েছে হিন্দুধর্ম। যেমন ‘ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু’ গ্রন্থের লেখক প্রফুল্ল সরকার লিখেছেন—‘তীক্ষ্ণবুদ্ধি ধীরমস্তিষ্ক ব্রাহ্মণ মনীষী ও ধর্ম্মাচার্যেরা অপূর্ব কৌশলে বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্মের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন।’
কিন্তু বাস্তবে সেটি ছিল রাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ মদদে সাম্প্রদায়িক উচ্ছেদের দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার ফসল। সেই ‘অপূর্ব কৌশলে’র একটি উদাহরণ কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক। তিনি সেতুবন্ধ থেকে হিমগিরি পর্যন্ত বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সমস্ত হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। এমনকি এই আদেশ প্রতিপালনে যে শৈথিল্য দেখাবে, তার জন্যও মৃত্যুদণ্ডের বিধান ঘোষণা করেছিলেন। ইতিহাসে রাজা শশাঙ্কের অনেক কৃতিত্বের মধ্যে বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম ধ্বংসের সার্বিক চেষ্টা এবং মগধের বৌদ্ধদের ওপর ‘অগ্নি ও তরবারি’ দ্বারা ভীষণ অত্যাচারের কথাও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গেই লিপিবদ্ধ হয়েছে।
এরপর অষ্টম শতকে হিন্দুত্বের পুনরুত্থানকালে কুমারিল ভট্ট তো রীতিমতো বৌদ্ধ নিপীড়নের যাথার্থ্য দান করেছিলেন শাস্ত্র উল্লেখ করে। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে—‘বৌদ্ধ মাত্রই বধ্য।’ মাদুরার রাজা শূলে চড়িয়েছিলেন আট হাজার জৈন পণ্ডিতকে। সপ্তম শতকে কুমায়ুনে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল বৌদ্ধধর্ম। অথচ শঙ্করাচার্যের আন্দোলন সেখানে একটি বৌদ্ধ মন্দিরকেও অবশিষ্ট রাখেনি। ‘বৌদ্ধধর্ম বিনাশ’ করার পরে অন্য অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণদের নিয়ে এসে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল প্রধান প্রধান মন্দিরের ভার।
এই সাম্প্রতিক অতীতেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিচলিত বোধ করেছেন এই কথা ভেবে যে, যে-পূর্ববঙ্গে এক কোটিরও বেশি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন, এবং বাস করতেন ১১,৫০০ বৌদ্ধভিক্ষু, সেই পূর্ববঙ্গে তিনি ৩০ বছর অনুসন্ধান চালিয়ে বৌদ্ধধর্মের একটি পুস্তিকার সন্ধান পর্যন্ত পাননি।
ইসলাম এই উপমহাদেশে এসেছিল সেই খেলাফতের যুগেই আরব-মুসলিম বণিক এবং সুফি ধর্মপ্রচারকদের হাত ধরে। তবে রাষ্ট্রক্ষমতায় ইসলামের আবির্ভাব মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে। আর বাংলায় এলো ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির অশ্বারোহী বাহিনীর পিঠে চেপে। তার আগে বল্লাল সেন চতুর্বর্ণ সমাজকে আরো বেশি বিভক্ত করেছেন। চার বর্ণে কুলাচ্ছিল না। করা হলো ছত্রিশ বর্ণ। ষোড়শ শতকে স্মার্ত রঘুনন্দন সেই ছত্রিশকে পরিণত করেছিলেন ২৩৬-এ।
সুদীর্ঘকাল মুসলিম শাসকরা এই উপমহাদেশে শাসন পরিচালনা করেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এটা প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে মুসলমান শাসকরা ছিলেন পুরোপুরি হিন্দুবিদ্বেষী এবং সাম্প্রদায়িক। এই দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং যদুনাথ সরকার। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে—‘সকল ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার যে উদার চেতনা হিন্দুরা প্রচার ও প্রয়োগ করে এসেছে তা এখনও সভ্য মানব সমাজের কাছে একটি আদর্শ।’ আরেকজন, আচার্য স্যার যদুনাথ সরকারের মতামত হচ্ছে—‘যে ধর্ম (ইসলাম) তার অনুগামীদের ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে শেখায় লুটতরাজ ও হত্যা সেই ধর্ম মানব সমাজের প্রগতি বা বিশ্বশান্তি—দুয়েরই পরিপন্থি।’
এই দলের মতামত এবং সিদ্ধান্তগুলির সারসংক্ষেপ করলে দাঁড়ায়—১. হিন্দুধর্ম উদার ও পরমতসহিষ্ণু। ২. ইসলাম ঠিক তার বিপরীত। ৩. হিন্দুধর্মের উদার আহ্বান উপেক্ষা করে দুই সম্প্রদায় চিরকাল বিচ্ছিন্ন থেকেছে ইসলামের অনুদারতার কারণেই। ৪. হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার সম্পর্ক বরাবরই ছিল তিক্ততার সম্পর্ক। ৫. মুসলমান শাসকরা ছিলেন সাম্প্রদায়িক। অস্ত্র হাতে স্বধর্ম প্রতিষ্ঠা ও বিধর্মী বিনাশই ছিল তাদের ব্রত।
আরেকদলের মতে, মুসলমান সম্রাটরা মোটেই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশি কিছুই করেননি তারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে। এই মত পোষণকারী দলের মধ্যে রয়েছেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, মুহম্মদ হাবিব, ইরফান হাবিব প্রমুখ।
প্রথমোক্ত দলের সপক্ষে যথেষ্টই যুক্তি রয়েছে। সুলতান মাহমুদের বর্বর বিধ্বংসী আক্রমণ— মথুরা, থানেশ্বর, কনৌজ, এবং সর্বোপরি সোমনাথের জগদ্বিখ্যাত মন্দির লুঠ ও ধ্বংসের কথা তাদের জানা। তারা জানেন ইসলামে আছে তরবারির মুখে ধর্ম প্রচারের কথা, দার-উল-ইসলাম এবং দার-উল-হারব-এর তত্ত্ব। তারা জানেন তথাকথিত ওলামাদের হিন্দুবিদ্বেষের কথা, তাদের জেহাদি কার্যকলাপের কথা, কাফি খান, বারানি প্রমুখ ঐতিহাসিকদের সঙ্কীর্ণতার কথা, ধর্মান্ধ ফিরোজ তুঘলক কিংবা আলমগীরের বহুবিধ কার্যকলাপ এবং অন্য ধর্মীয়দের ওপর জিজিয়া কর আরোপের কথা।
কিন্তু অনেক প্রশ্নেরই আবার কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। যেমন মুহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধুজয়ের পরে যে মন্দিরগুলি ভেঙেছিলেন, সেগুলি তাকে আবার গড়ে দিতে হয়েছিল কেন? যে আলমগীরকে চরম হিন্দুবিদ্বেষী বলে জানা যায়, সেই আলমগীর উমানন্দের মন্দির তৈরির জন্য জমি দান করছেন কেন? আবার ধর্মবোধই যদি মূল চালিকাশক্তি হয়ে থাকে, তাহলে সিকান্দার লোদীই বা কেন জৈনপুরে হিন্দু মন্দিরের ওপর গড়ে ওঠা সকল মসজিদ ধ্বংসের আদেশ দিলেন? যে সুলতান মাহমুদ হিন্দুবিদ্বেষী হিসেবে ঘৃণিত, সেই মাহমুদের হিন্দু সৈন্যরা কেন তার হয়ে মধ্য এশিয়ায় লড়াই করেছে? মাহমুদের বিরুদ্ধে তার প্রধান সেনাপতি নিয়ন্তিজিন বিদ্রোহ করেছিলেন। সেই বিদ্রোহ দমনে সুলতান মাহমুদ যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন, তার সেনাপতি ছিলেন হিন্দু ধর্মের অনুসারী তিলক। এটি কীভাবে ঘটল?
বাবর মৃত্যুর সময় পুত্র হুমায়ুনের জন্য ছয়টি আদেশ রেখে যান। সেগুলির সার কথা হচ্ছে—‘বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করে ভারতে। এই দেশের সরকারের গুরুদায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত হচ্ছে এর জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। কখনো ধর্মীয় সংস্কার যেন তোমার মনকে প্রভাবিত না করে। সমস্ত সম্প্রদায়ের দেশবাসীর ধর্মীয় স্পর্শকাতরতা ও ধর্মীয় আচার আচরণের প্রতি প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধার ভাব রেখে নিরপেক্ষ বিচার করবে।’ মুসলমানীত্বের নাম করে ভারত দখল করার পরে এই রকম পরধর্মসহিষ্ণুতার উপদেশ কেন? সমাজের নিচের তলায় বসবাসকারী মানুষ ইসলামের সাম্যের বাণীর কারণে নাহয় ধর্মান্তরিত হয়েছিল? কিন্তু সিংহাসন দখলে রাখার জন্য রাজা গণেশের ছেলে যদুর জালালউদ্দিনে পরিণত হওয়া কিসের ইঙ্গিত করে? বেরিলির ধরম রায় ফৌজদারকে চিঠি লিখে জানাচ্ছেন যে তার কাকাকে দেওয়া জমিদারি তাকে দিলে তিনি মুসলমান হতে রাজি। জমিদারি এবং মনসবদারি পেলে রাজা কাল সিং, দেবী খাত্রী, মাত্রুক, কেশরী, শিউ দত্ত, জ্বালানাথ, ভগবান দাসের পুত্র রামানন্দ—এরা সবাই মুসলমান হয়েছিলেন মনসবদারির বিনিময়ে। ঘোড়াঘাট দুর্গের অধ্যক্ষ ভান্দসী রায়ের অভিযোগে বারবাক শাহ নিজের প্রিয় পাত্র ইসমাইলকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন কেন? ১৫৯৪-৯৫ সালে ১২টি আঞ্চলিক অর্থমন্ত্রীর মধ্যে আটজনই হিন্দু ছিলেন কেন? জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহনের তৃতীয় বছর থেকেই অমুসলিম মোহন দাস সম্রাটের দেওয়ান হিসেবে দায়িত্ব পেলেন কেন? শাহজাহানের রাজত্বকালে রায় চন্দ্রভান সচিবালয়ের প্রধান ছিলেন কেন?
এইসব প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এমন হতে পারে যে সাম্রাজ্য পরিচালনার প্রয়োজনে যোগ্য অমুসলিমদের নিয়োগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তারা। আবার একই সঙ্গে এই সিদ্ধান্তেও আসা যেতে পারে যে ভেতরে ভেতরে সাম্প্রদায়িক হলেও বাইরে একটি সম্প্রীতির বাতাবরণ, অন্তত দেখানোর জন্য হলেও, প্রয়োজন ছিল মুসলমান সম্রাটদের।
তবে একটা ব্যাপারে সবাই একমত যে, শ্রমজীবী কোটি কোটি প্রজাদের শোষণ করার ব্যাপারে প্রত্যেকেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সম্রাটের অনুগ্রহভাজন আমির খসরুকেও তাই বলতে হয়েছিল যে—‘সম্রাটের মুকুটের প্রতিটি মুক্তা আসলে দরিদ্র মানুষের জমাট বাঁধা রক্ত এবং কান্না দিয়ে তৈরি।’
কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপমহাদেশের ইতিহাস শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস না হয়ে পরিণত হয়েছে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতারই ইতিহাস।
০৩.
দেখা যাচ্ছে এই বিষয়টি নিয়ে শান্তনু কায়সার যতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, তাতে উত্তরের চাইতে প্রশ্নের সংখ্যা বেশি। বেঁচে থাকলে উত্তর অনুসন্ধানে অবশ্যই ব্যাপৃত থাকতেন শান্তনু কায়সার। এখন তিনি নেই। তাই দায়ভারটা আমাদের কাঁধে।





















 জাকির তালুকদার
জাকির তালুকদার

















