ব্রেক্সিট
দক্ষিণ এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপের ঐক্য
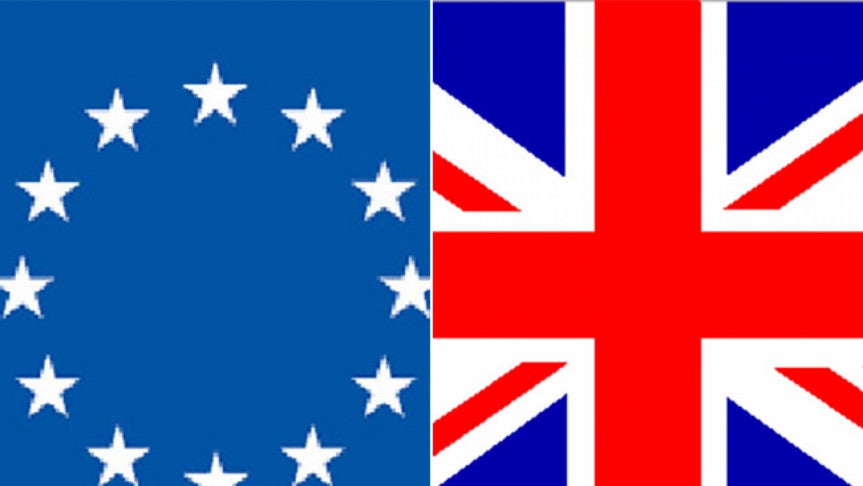
ব্রিটেনে হয়ে গেল গণভোট। এটি ছিল গণতন্ত্রের এক ব্যতিক্রমী উৎসব। ইউরোপীয় ইউনিয়নে দেশটির থাকা না থাকার প্রশ্নে ক্ষমতাসীনরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার দুঃসাহস দেখানোর আগেই ফিরে গেছেন জনগণের আদালতে। এই গণভোটকে ব্যতিক্রম বলা হলেও বাস্তবে তা বলা যায় না। হয়তো এটা বাংলাদেশ কিংবা দক্ষিণ এশিয়ার চোখে ব্যতিক্রম। কিন্তু ইউরোপের গণতন্ত্রে এটি নতুন নয়। বছর দুই আগে (১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪) খোদ ব্রিটেন থেকেই বেরিয়ে যাওয়া বা না যাওয়ার প্রশ্নে গণভোট হয়েছিল স্কটল্যান্ডে। স্কটল্যান্ড বর্তমানে ব্রিটেনের অধীনে থাকা একটি বিশেষ অঞ্চল যা গোটা যুক্তরাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ। সেই ভোটে ‘না’ জয়যুক্ত হয়েছিল। স্কটল্যান্ডের ৫৫% জনগণ নিজেদের সার্বভৌম স্কটিশ সীমানা অর্জনের বিপরীতেই ভোট দিয়েছিলেন। তাঁরা যুক্তরাজ্যের অংশে থাকাকে নিজেদের জন্য মনে করেছিলেন কল্যাণকর।
লক্ষণীয় বিষয় হলো, ৪৫% মানুষ চেয়েছিলেন একটি স্বাধীন স্কটল্যান্ড। তাঁরা চেয়েছিলেন, ব্রিটিশ রানির আধিপত্যকে বিদায় জানাতে। তাঁরা বিজয়ী হননি। তবে সেখানে বিজয়ী হওয়া ৫৫% লোক পরাজিতদের পিটিয়ে বের করেও দেননি। উভয়ই বসবাস করছেন একে অপরের ভিন্ন মতকে সম্মান করেই। ইউরোপের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় মাহাত্ত্ব এটাই। সেখানে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় রক্তপাত হয় না। এবার ইইউ প্রশ্নে যুক্তরাজ্যের গণভোটের রায়ে জিতে গেল ‘হ্যাঁ’। প্রায় ৫২ শতাংশ ভোটার ইউরোপ ছেড়ে যাওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। তার মানে ‘ব্রেক্সিট’ বাস্তবায়ন হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ব্রিটেন। আগামী দুই বছরের মধ্যেই এটি কার্যকরের আইনি প্রক্রিয়া শুরু হবে। দুটি নির্বাচনের মধ্যে সম্পর্ক এক জায়গায়। তা হলো, জনগণের মতের প্রতিফলন। এমনকি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন, যিনি ব্রেক্সিটের বিপক্ষে ছিলেন এবং এই প্রশ্নে গণভোটের ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি গণভোটের পরপরই পদত্যাগ করেছেন। এই ঘটনাকে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা হিসেবেই দেখা যেতে পারে। আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য, ব্রেক্সিটের পক্ষে-বিপক্ষে এই গণভোট মূলত ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি বিষয়। যেমন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার সংগঠন সার্ক সম্পৃক্ত। পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত একটি বিষয়ে গণভোট আহ্বান আর তাতে ব্রিটিশ জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রমাণ করে পররাষ্ট্রনীতিতে জনসম্পৃক্ততার বিষয়টি। পক্ষান্তরে, আমাদের মতো উন্নয়নশীল বিশ্বে, পররাষ্ট্রনীতিকে ধরা হয় রাষ্ট্রীয় এলিটদের কাজ। জনগণের সম্পৃক্ততা সেখানে থাকে কেবলই যুদ্ধের সময়!
ব্রেক্সিট গণভোটের বিশ্লেষণ করতে হলে ২০১৪ সালের স্কটল্যান্ডের গণভোটকে সামনে রাখতে হবে। ফলাফলে একটি ‘না’ এবং অন্যটিতে ‘হ্যাঁ’ বিজয়ী হয়েছে। মূলত, এই দুই গণভোটের ফলাফল একসঙ্গে করলে দাড়ায়, ‘জাতিরাষ্ট্র’ হিসেবে যুক্তরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য টিকিয়ে রাখতে অধিকাংশ জনগণ আপাতত আগ্রহী। একদিকে যেমন যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরের স্কটিশ জনগণ চায়নি দেশটি ভেঙে যাক। অন্যদিকে গোটা দেশের জনগণ এটাও চায়নি যে, দেশটি বৃহত্তর ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজের অর্থনীতি, সীমানা ও সার্বভৌমত্বের ওপর ক্ষমতা হ্রাস করুক।
দ্বিতীয় যে বিষয়টি লক্ষণীয়, দুটি গণভোটের ক্ষেত্রেই জয়-পরাজয়ের ব্যবধান খুবই সামান্য। যাদের মতামত পরাজিত হয়েছে তারাও সংখ্যায় ক্ষুদ্রকায় নয়। অর্থাৎ একদিকে ব্রিটেনের মধ্যেই স্কটিশ ‘স্বাধীনতাবাদ’ বা ‘শান্তিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদ’ ব্যাপক সক্রিয়; অন্যদিকে ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পক্ষে বিরাট একটি জনমত আছে। ওপরের দুটি বিষয়কে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলে গ্রেট ব্রিটেনে বড় দাগে তিন ধরনের মতামতের উপস্থিতি পাওয়া যায়। এক. স্কটিশ ও ইংরেজ জাতীয়তাবাদ; দুই. ব্রিটিশ জাতিরাষ্ট্রবাদ এবং তিন. ইউরোপীয় ইউনিয়নবাদ।
আরেকটি বিষয় লক্ষ না করলে ভুল হবে। তা হলো, স্কটিশরাই বেশির ভাগ ব্রেক্সিটের বিরোধিতা করেছিল। তার মানে, ইংরেজ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে স্কটিশ জাতীয়তাবাদ আর ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের সমর্থকদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। অন্যভাবে বললে, স্কটল্যান্ডের নাগরিকরা ব্যাপক হারে চেয়েছিল ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকুক। যারা ২০১৪ সালে স্বাধীন স্কটল্যান্ডের পক্ষে ছিলেন তাঁরাও চেয়েছেন, আবার যাঁরা ঐক্যবদ্ধ ব্রিটেন চেয়েছিলেন তাঁরাও। অর্থাৎ, ব্রিটেনের এবারের গণভোটে আবারও স্কটিশ জনগণের জনমতের প্রতিফলন হয়নি। স্বভাবতই, এই বঞ্চনা তাদেরকে ফের বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করতে পারে। মোটকথা, আপাতত ইউরোপীয় রাজনীতির এক বড় পরিবর্তনের সূচনা করল ব্রিটেনের এই গণভোট।
প্রশ্ন হলো, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে এই গণভোট কী কী প্রভাব ফেলবে। স্বল্প মেয়াদের প্রভাবগুলো এরই মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হতে শুরু করেছে। পাউন্ডের দরপতন শুরু হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ইউরোর দরও পতন হবে। ইউরো ও পাউন্ডের এই দরপতন সারা বিশ্বের অর্থনীতিতেই প্রভাব ফেলবে। ইউরোপজুড়ে বিভিন্ন দেশের রক্ষণশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠী নতুন করে প্রচারণা শুরু করেছে আরো কতগুলো গণভোটের। বলা হচ্ছে, স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডে এবার গণভোট হলে তাদের বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে গ্রেট ব্রিটেন থেকে। এর মাধ্যমে শত শত বছরের গ্রেট ব্রিটেন তার গ্রেটনেস হারিয়ে বসতে পারে। জন্ম নিতে পারে নতুন জাতিরাষ্ট্র। ওদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য সুইডিশরা ‘সুয়েক্সিট’, জার্মানরা ‘জারেক্সিট’, নেদারল্যান্ডসের কিছু নেতা ‘নেক্সিটের’ দাবি তুলছেন। একই দাবি তুলেছেন ফ্রান্সের ‘ন্যাশনাল ফ্রন্ট’ দলের এক নেত্রী। এই সব তথ্য নির্দেশ করছে যে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংকটের মুখে পড়তে যাচ্ছে। অবশ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের প্রতিক্রিয়া এখানে খুবই গঠনমূলক। তারা তিনটি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এক, হতাশা : ব্রিটেনের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায়; দুই, শ্রদ্ধা : ব্রিটিশ জনগণের অধিকাংশের মতামতের প্রতি; তিন, সমাধান : আর কেউ যাতে বেরিয়ে না যায়। বাস্তবে কী হতে চলেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যাবে ওই সব দেশে কবে গণভোট হয় আর তার ফলাফল কী দাঁড়ায় তার ওপর।
স্বল্প মেয়াদে এসব প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি, দীর্ঘমেয়াদে এই গণভোট যে প্রভাব সৃষ্টি করছে তা হলো, এর মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতার রোল মডেল হিসেবে ইউরোপের যে নাম-ডাক ছিল, যাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় সচরাচর ‘ইউরোসেন্ট্রিসিজম’ বলা হয়, সেটি প্রশ্নের মুখে পড়ল। ইউরোপ আর আঞ্চলিকতাবাদের স্বার্থক উদাহরণ রইল না। কার্যত এটা ‘আঞ্চলিকতাবাদের ক্রমহ্রাসমান অধ্যায় (Declining Wave of Regionalism)’ শুরু করল। পরন্তু, অল্প ব্যবধানে নির্বাচনগুলোর ফলাফলের মাধ্যমে ধারণা করা যায় যে, গণতান্ত্রিক বিশ্বের রাজনীতিতে তীব্র মেরুকরণ সৃষ্টি হচ্ছে। কট্টরপন্থীদের বিজয়ী হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে। কার্যত, মুখোমুখি রাজনৈতিক পক্ষগুলোর অধিকাংশই নিজ নিজ অবস্থানে কট্টর বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। মধ্যপন্থা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে, সমঝোতার প্রবণতা কমছে। যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর সেই বার্তাটি আরো স্পষ্ট হওয়া যাবে। সর্বোপরি, এই গণভোটের সবচেয়ে বড় দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব হচ্ছে অর্থনীতিতে। একটি অর্থনৈতিক জোট হিসেবে ইউরোপের যে সাফল্যের জয়জয়কার শোনা যাচ্ছিল, তা প্রশ্নবিদ্ধ হলো। এখন একটি আঞ্চলিক জোট হিসেবে কাস্টমস ইউনিয়নের (Customs Union) অধীনে ইউরোপের বাণিজ্য ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে হবে।
শেষ কথা হলো, স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদে এসব প্রশ্ন মূলত ইউরোপীয়দের নিজস্ব। হয়তো, বিশ্বায়নের ফলে ইউরোপের কোনো সংকট দক্ষিণ এশিয়াসহ অন্যান্য অঞ্চলকেও প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু মৌলিকভাবে এই সংকট সৃষ্টিতে দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দায় নেই। এবং এ থেকে উত্তরণেও দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর কোনো ভূমিকা মুখ্য নয়। আমরা কেবল অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারি। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক উন্নয়নে পারস্পারিক সহযোগিতার লক্ষ্যে সার্ক নামে যে সংস্থাটি রয়েছে তা ইউরোসেন্ট্রিক আঞ্চলিকতার মডেল নিয়ে পুনর্ভাবনা করবে কি না- সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। স্পষ্টতই, সার্কভুক্ত দেশগুলো সাফটা চুক্তির আওতায় একটি মুক্ত বাণিজ্যিক এলাকা (Free Trade Area)-এর দিকে ধাবিত হচ্ছে। বাস্তবতা হলো, এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও বৃহৎরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিশালাকার বাণিজ্য ঘাটতির ক্রমবর্ধমান হার এবং নির্ভরশীলতার অসমতা এই মুক্ত বাণিজ্যিক এলাকার প্রকল্পকে বাধাগ্রস্ত করছে। এ অবস্থায়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই বাস্তবতা থেকে সার্ক নেতাদের শিক্ষা নেওয়া জরুরি।
লেখক : গবেষক ও সংবাদকর্মী





















 জাকারিয়া পলাশ
জাকারিয়া পলাশ


















